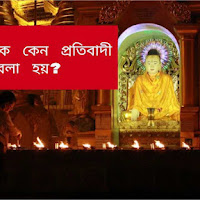বৌদ্ধধর্মকে কেন প্রতিবাদী বলা হয়?
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতে ধর্মীয় আলোড়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই যুগে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ দেখা যায় ও বহু নতুন ধর্মমতের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে এই যুগে ভারতে ৬৩টি প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটে। এই সর্ব ধর্মমতের মতে, বৌদ্ধধর্ম ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বহু পূর্বেই বৈদিক ধর্ম তার সরলতা ও পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ, পশুবলি, দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, ধর্মীয় কার্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অপরিহার্যতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ও ক্রমবর্ধমান দক্ষিণার চাহিদা প্রভৃতির ফলে ধর্ম প্রাণহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বৌদ্ধদর্শনে যাগযজ্ঞ অপেক্ষা আত্মার মুক্তি, কর্মফল ও স্বাধীন চিন্তার আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, এইসব কারণে সমাজে নতুন ধর্মীয় চিন্তা ও আদর্শের পথ প্রস্তুত হয় এবং সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ওল্ডেনবার্গ বলেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক শত বছর পূর্বেই ভারতীয় চিন্তার জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, যা বৌদ্ধধর্মের পথ প্রশস্ত করে।
আপনি চাইলে এগুলো পড়তে পারেন
বৈদিক সমাজ স্পষ্টতই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। সমাজে জণদের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা বহু সুযোগ-সুবিধা পেতেন তাদের কোন কর দিতে হতো না এমনকি তারা ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়দের হাসান। তাঁরা ছিলেন যোদ্ধা ও শাসকশ্রেণির মানুষ। এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা
এবি পেলেও বৈশ্যদের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং অনেক সময় তাদের শূদ্রদের সঙ্গে এক এর দেখা হত। শূদ্রদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, বহুক্ষেত্রে তাদের অস্পৃশ্য জ্ঞান আহত। সমাজ ও ধর্মে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য শক্তিশালী ক্ষত্রিয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই কারণে সমাজে শ্রেষ্ঠত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ৫৭ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজবংশীয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। সমাজে পতিতারা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হত। অপরদিকে গৌতমবুদ্ধ নারীসমাজ, পতিতা, দস্যু সকলকেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এর ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নতুন ধর্ম চিন্তার উন্মেষে উত্তর-পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য গরুপালন ছিল অপরিহার্য। অথচ বৈদিক ধর্মরীতিতে বলিদান ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং, এই নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে স্থায়ী করার জন্য নির্বিচারে পশুহত্যা বন্ধ করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কৃষির আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে কৌশান্তি, কোশল, কুশীনগর, বৈশালী রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি বহু নতুন নতুন নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।
এইসব নগরগুলিতে অসংখ্য কারিগর ও ব্যবসায়ী বসবাস করত। এই সময় তারা মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেছিল, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তারা যথেষ্ট ধনবান হয়ে উঠে। অথচ বৈদিক আদর্শে পরিচালিত সমাজে ধনবান বৈশ্যদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তারা এমন এক ধর্মের সন্ধানে ছিল যা তাদের মর্যাদা দিতে সক্ষম। বলা বাহুল্য বৌদ্ধধর্ম তাদের এই প্রয়োজন মেটায়, কারণ এই ধর্মমতে জাতিভেদ প্রথার কোনো স্থান ছিল না। এই কারণে বৈশ্যরা বৌদ্ধধর্মের প্রবল সমর্থকে পরিণত হন।
ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে টাকা ধার দেওয়া, সুদ গ্রহণ করা, সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয় ও পাপ বলে বিবেচিত। বহুশ্রেষ্ঠী মহাজন সুদের কারবার করত এবং এটাই ছিল অনেকের জীবিকা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এগুলি ঘৃণার চোখে দেখত এবং সমাজের চোখে এই সমস্ত ব্যক্তিরা অপরাধী বলে চিহ্নিত হত। স্বভাবতই বৈশ্যরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে এবং বৌদ্ধধর্মকে সমর্থন করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।
এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধন সম্পদের প্রাচুর্য, আড়ঙ্গণ পূর্ণ জীবনযাত্রার একশেণীর মানুষের মনে প্রবল ব্রিটিশনার সঞ্চার করেছিলেন বিলাসিতার জীবনযাত্রা ত্যাগ করে পূর্বের সহজ, সরল ও তপশ্চর্যার জীবনে ফিরে যেতে চাইছিল। বুদ্ধদেব এই বিলাসিতার পরিহার ও তপস্বীর জীবনযাত্রার কথা প্রচার করে মানুষের চাহিদাও মিটিয়েছিলেন। বেশ সন্ন্যাসীরা শরীর ও আত্মাকে তৃপ্ত রাখার জন্য যতটুক প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে পারতেন।
ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এই যুগে কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজের প্রসারের ফলে এক শ্রেণির মানুষের হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয় এবং অপর শ্রেডি অবস্থা ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে আসে। সমাজের বৃহত্তর অংশের লোকেরা ছিল দরিদ্র বদিত ও নিপীড়িত। ধনবন্টনের কোনো ব্যবস্থা বৈদিক সমাজে ছিল না। এরফলে ধনী একদিকে যেমন ধনীই হত এবং দরিদ্র দিন দিন দরিদ্রতর হত। এজন্য বলা হত এসবই কর্মফল। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় বুদ্ধদেব দরিদ্র শ্রেণিকেও সহানুভূতি ও অধিকার দান করে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে, দরিদ্রই দর্নীতি ও সব অপরাধের উৎস। তাই অপরাধ দূর করতে হলে উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষক, শ্রমিক ও বণিকদের হাতে দিতে হবে। এইভাবে তিনি সমাজের নিম্নসাজ মানুষের মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়েছেন। ভোগবিলাস ও সন্ন্যাসের মধ্যবর্তী এর 'মধ্যপন্থা'র সন্ধান দিয়ে সমাজকে রক্ষা করেন সমাজের এই বিভিন্ন দিক, যথা- ধর্মীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈষম্য, দুর্নীতি, ব্যাভিচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বা বিকল্প পথের অনুসন্ধান হিসেবে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ঘটায়, তাই বৌদ্ধধর্মকে প্রতিবাদী ধর্ম বলা হয়।