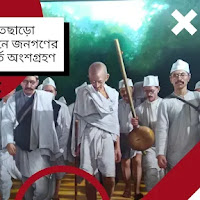ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে অথবা, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল নাকি অথবা, সংঘটিত এই আন্দোলন কি বিপ্লব বলা যায় বা, সংঘটিত ভারতছাড়ো আন্দোলনের পর্যায়ে গুলি আলোচনা করো

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে সারা দেশ চরম হতাশা ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। গান্ধীজী, তার বিখ্যাত হরিজন পত্রিকায় লিখতে থাকেন যে, জাপানের আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটেনের উচিত অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করা, ব্রিটেনের উপস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।ব্রিটেনের ভারত ত্যাগের পরেও যদি জাপান আক্রমণ করে তবে ভারতবাসী তা নিজেরাই প্রতিরোধ করবে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত-ছাড়ো প্রস্তাব অনুমোদন করে, কংগ্রেস সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, যদি ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাহলে ভারতবাসী কেবলমাত্র ভারতের স্বার্থে নয়- ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও অপরাপর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য ব্যাপক ও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবে।
কংগ্রেসে নেতৃবৃন্দের একাংশের দ্বিমত সত্বেও গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে ৮ ই আগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভারতছাড়ো প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। গান্ধিজী দুপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন "এই মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক নরনারী নিজেকে স্বাধীন মনে করবে, মনে রাখতে হবে আমরা কেউই সাম্রাজ্যবাদের পদানত নই।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যে গান্ধীজি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের গ্রেফতার করা হয় এবং কংগ্রেস দলকে সরকার বেআইনি বলে ঘোষণা করেন ৷ ফলে পরের দিনেই ৯ আগস্ট থেকে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ,ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিদের নেতৃত্বে বাংলায়, যুক্তপ্রদেশে, বিহার গুজরাটে স্থানীয় নেতারা নিজেদের মতো করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় ৷ ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন তাই প্রথম সারির নেতৃবৃন্দদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্রিটিশ বিরোধী এবং তীব্রতার আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৷
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাপানি আক্রমণের ভীত এবং ব্রিটিশ সরকারের তীব্র দমনমূলক নীতির ফলে জনগণের মধ্যে এক আংশিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল ৷ আগস্ট মাসে হয়েছিল বলে এই আন্দোলনকে অনেকে আগস্ট আন্দোলন বলে ৷ ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা, ব্রিটিশদের অমনোভাব, কংগ্রেসকে আন্দোলন মুখী করে তোলে ৷ তবে এই আন্দোলন কে কখনোই একে বিপ্লব বলা সঙ্গত নয় বলে বেশিরভাগই ঐতিহাসিক মনে করেন ৷ যেহেতু ৯ই আগস্ট ভোরে প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ও গ্রেপ্তার হওয়ার পর ভারতছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ববিহীন ভাবে চারিদিকে প্রসারিত হয়, তাই অনেকে ঐতিহাসিকের ধারণা এই আন্দোলন একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন অর্থাৎ নেতৃত্বের নেত্রী হীন একটি আন্দোলন মাত্র ৷
যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিক থেকে দেখা যায় তাহলে কোন সন্দেহ নেই এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ৷ গান্ধীজী অহিংস আন্দোলনে ডাক দেন ৷ রাজা গোপালাচারি ছাড়া কংগ্রেসের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতারা সকলে এই প্রস্তাবকে ঐক্যবদ্ধ হন ৷ গান্ধীজীর ধারণা ছিল জার্মানি ও জাপান জিতবে সেই গান্ধীজি ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অপমাহীন গণ সংগ্রামের ডাক দিলেন ৷ সুমিত সরকার লিখেছেন যে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব ছিল খুবই অস্পষ্ট আন্দোলনের খুঁটিনাটি বিষয় ও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । তিনি মনে করেন আসলে মোটা ব্যাপারটা ছিল বিশেষ কার্যপদ্ধতি অনুসরণকালে সীমানায় পৌঁছানোর একটি প্রয়াস ।
ব্রিটিশরা অবশ্যই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে আগস্ট মাসে কংগ্রেস একটি স্বতন্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করবে কিন্তু, এর কোন প্রমাণ নেই ৷ আধুনিক গবেষকরা লিখেছেন যে এই আন্দোলন পূর্ববর্তী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ছিল ৷ কিন্তু যদি আমরা আঞ্চলিক দিক থেকে দেখি তাহলে এই আন্দোলনকে সেই অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যাবে না । আন্দোলনে চারটি ঝটিকা কেন্দ্রে বিহার , যুক্ত প্রদেশ, মেদিনীপুর অঞ্চলে আন্দোলনের চরিত্র এক নয় ৷ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে আঞ্চলিক স্তরের নেতারা নিজেদের মতো করে চালিত সংঘটিত করেছিল ৷ ঐতিহাসিক দীপাণ চন্দ্র লিখেছেন যে," এই আন্দোলনের রাজনৈতিক মূল্য কম ছিল, এই আন্দোলন স্বাধীনতার দাবি কে আলোচ্য বিষয় পরিণত করেছিলেন ৷ তাই আন্দোলনটি শুরু শুধু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয় এটি একটি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ বিপ্লব ৷"
অধ্যাপক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন," ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে অসংগঠিত বলা যাবে না তার কারণ জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সর্বোচ্চ যে শাখা-প্রশাখা গড়ে তুলেছিল তাতেই জাতীয়তাবাদের সংগঠনিক ভিত্তি বিনষ্ট হয়েছিল ৷ ১৯৪২ এর আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আঙ্খকাকে তুলে ধরেছিল ৷ এই সময় জাতীয় কংগ্রেসরে বিকল্প হিসাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আন্দোলন পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ তাই প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৯৪২ এর আন্দোলন প্রাসঙ্গিক স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷" তবে আবার আরেকটি স্তরে অন্য একটি পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায় ৷ এই দৈত্যরূপের ফলে শেষ পর্যন্ত তা ধারাবাহিক হতে পারেনি । গান্ধীজীর অনুমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মিত্র পক্ষ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ৷ ভারতছাড়ো আন্দোলনকে তাই এক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত অহিংস আবার অন্য দিক থেকে পরিকল্পনা যুক্ত আঞ্চলিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ এক গভীর ব্যাপক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ৷
সাম্প্রতিক আঞ্চলিক গবেষণা ও নানা সূত্র থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে আন্দোলনের একটি যথার্থ প্রকৃত চরিত্র সাফল্য এবং ব্যর্থতার অবিমিশ্র ইতিহাস ৷ এই আন্দোলনের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য এ কথা নিশ্চিত যে গান্ধীজীর আপসহীন ও অনমনীয় মনোভাব জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল ৷ সুমিত সরকার লিখেছেন যে এই আন্দোলনে গান্ধীজীর কোন কর্মসূচি ছিল না ৷ এই প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয়েছিল এখনো সময় আসতে পারে যখন কোন নির্দেশ জারি করা এবং তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ ভারতছাড়ো আন্দোলন স্বাধীনতা দাবিকে অস্বীকার করতে পারেনি । অহিংসবাদী গান্ধীও তাই সন্ততন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল ৷ ম্যাক্স হার্কোট দেখেছেন যে ভারতছাড়ো আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও উচ্চবর্ণের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলেন ৷
রনজিত গুহ সম্পাদিত সম্প্রকালীন "A Subaltern Studies Reader, 1986-1995" এর দ্বিতীয় খন্ডে লেখা হয়েছে ভারতছাড়ো আন্দোলনের দুটি বিপরীত ধর্মীয় স্রোত প্রবহমান ছিল ৷ একদিকে ছিল উচ্চবর্ণের ধনী চাষীদের ভূমিকা, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিদদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ,অন্যদিকে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোল ৷ ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, 1942 এর আন্দোলন ছিল মূলত সৈনিকদের যুদ্ধ সেনাপতিরা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু সৈনিকদের ভূমিকা ছিল গৌরব জনক ৷ কারণ তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে ৷
ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল কিনা বা এই আন্দোলনের পিছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল কিনা! এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল । ব্রিটিশ সরকার অচিরেই অনুভব করেছিল যে এই আন্দোলন দমন করতে না পারলে ভারতে তাদের দিন আসন্ন। আমাদের মনে রাখা দরকার আন্দোলন ভালোভাবে শুরু হওয়ার আগেই গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা কারাবন্দি হন । গান্ধীজী আন্দোলন সংগঠিত করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি। একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণ আন্দোলনকে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। মূলত এ সময় সমস্ত ভারতবাসী যেকোন আন্দোলনের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল। তারা যেন বেপরোয়া ভাবে আহ্বানের জন্য তৈরি হয়েছিল। মূলত এই ভারত ছাড়ো আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার চরমতম নিদর্শন । এ কথা ঠিক যে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল তবে বিফল হলেও একেবারে নিষ্ফল ছিল না। এইসব মন্তব্যের ভিত্তিতেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলে তার ভূমিকা কে ছোট করা যাবে না ।"