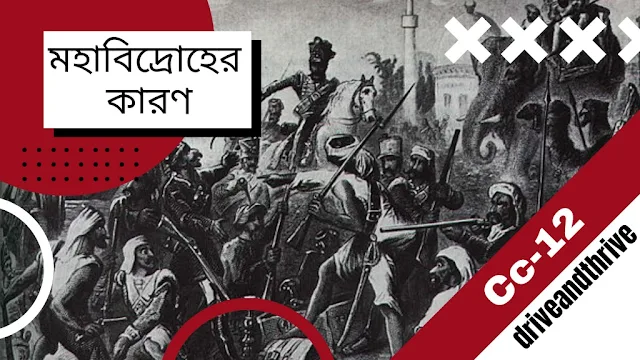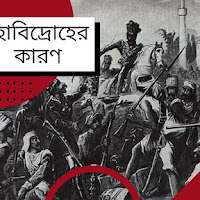মহাবিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
১৮৫৬ লর্ড ক্যানিং ভারতের বড়লার্ড জেনারেল নিযুক্ত হতে আসেন । তাঁর শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৮৬৭ সালের গণ-অভ্যুথান । এই ঘটনার নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মত আছে । এই ঘটনাটি সরকারী বিবরণে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত । অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের একদল এই ঘটনাকে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন । আবার আর একদল এই অভ্যুত্থানকে সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন । এই মতবিরোধিতার কারণে ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ- বিরোধী অভ্যুত্থানকে এই গ্রন্থে "১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ" বলে অভিহিত করেছেন ৷
আপনি চাইলে এগুলো পড়তে পারেন
১৯৮৭ সালে উত্তর ও মহাভারতে যে বিপ্লটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটে তা ব্রিটিশ শাসনের প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় । কোম্পানির সেনাবাহিনীর মধ্যে এই অভ্যুত্থান শুরু হয়ে তা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । প্রায় এক বছর, সৈনিক রাজাদেরী বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাদের সাহসিকতা ও আত্মবিসর্জন ভারতবাসীর ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।
এই মহাবিদ্রোহ শুরু যে ভারতের সেনাদের অসন্তুষ্ট ও ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এমন নয় । প্রকৃতপক্ষে এর মূল ছিল কোম্পানির প্রশাসন ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ এর প্রকাশ ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই বিক্ষোভ দানা বেড়ে উঠেছিল তাই থেকেই মহা বিদ্রোহের সূত্রপাত ৷
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মূলে বিভিন্ন কারণ ছিল-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক। ১৮৫৭ সালের অনেক আগে থেকেই দেশীয় নৃপতিরা উত্তরোত্তর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার সম্মিলিত চেষ্টা দু'বার হয়েছিল। মহীপুর অধিপতি হাজদার আলির নেতৃত্বে মহীপুর, হায়াবাদ ও মারাঠা এই তিন রাজ্যের মিলিত একটি বিশক্তি সংথ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা ওয়ারেণ হেস্টিংস-এর কূটনীতির ফলে ভেঙ্গে যায় ।
লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ ও সংযুক্তিকরণ নীতি দেশীর রান্দাদের মনে আশঙ্কা ও ব্রিটিশদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্রেক করেছিল। স্বরবিদোপ-নীতির প্রয়োগ করে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাধাদাভুক্ত করা হয়েছিল। তাজোর ও বর্ণটিকের রাজাদের বৃত্তি ও নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নানাসাহেব ছিলেন মারাঠাদের শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাদীরাও-এর দত্তকপুত্র। ১৮০৫১ রীষ্টাব্দে বাজীরাও-এর মৃত্যু হলে তাঁকে দেওয়া বৃত্তি থেকে ইরোদ সরকার নানাসাহেবকে বঞ্চিত করেন। সেইভাবে ঝাঁসির রাজার মৃত্যু হলে রানী লক্ষ্মীবাই-এর দত্তকপুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । এছাড়া ডালহৌসী মোগল সম্রাটের খেতাব বিলুপ্ত করে কোম্পানিকেই ভারতের সার্বভৌম শক্তি হিসাবে জাহির করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । কিন্তু ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়ার ডালহৌসী তা কার্যকর করতে পারেননি | কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।
ইংরেজ ঐতিহাসিক জন কে (John Kaye) লিখেছেন, ভোঁসলে রাজপ্রাসাদের সমস্ত আসবাবপত্র, মণি-মুক্তা, অলংকার এমনকি হাতী, ঘোড়া পর্যন্ত লুঠ করা হয়েছিল এবং এগুলির কিছু কিছু কলিকাতায় সকলের সামনে বিক্রি করা হয়েছিল । জন কে-এর ভাষায় এইসব অপকর্ম সাধারণ মানুজের মনে বিররূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ।
অযোধ্যার নবাব ও রাজপরিবারের অদৃষ্টেও একই নীতির ও কর্মের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদও লুঠ করা হয়েছিল। ওয়েলেসলির সময় থেকে অযোধ্যার নবাবরা ব্রিটেনের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেননি । জন কে-এর ভাষায় "False to their People false to their manhood they (Nawabs) were true to the British Government"। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডালহৌসীর পররাজ্য গ্লাসনীতির হাত থেকে অযোধ্যা রক্ষণ পায়নি । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে অযোধ্যার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে সেই রাজ্যের সবশ্রেণী-জমিদার, তালুকদার, মূললিম অভিজ্ঞাত, সৈনিক, ব্যবসায়ী ও কৃষক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিক্রিয়া শুধু অযোধ্যাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না- ভারতের সব দেশীয় রাজাদের মধ্যেও তা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের একনিষ্ঠ আনুগত্য সত্ত্বেও ব্রিটিশদের পররাজ্য গ্লাসের ক্ষুধা মেটেনি । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল রাজবংশ থেকে সম্রাট বা রাজা খেতাব তুলে নেওয়া হবে । এই ঘোষণা মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের মনে বিরাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নাই ৷
মহাবিদ্রোহের মূলে অর্থনৈতিক কারণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ । ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণ ও ভারতের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক বনিয়াদের জনসাধনের ফলে কৃষক, শিল্পী, পূর্বতন জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য শ্রেণী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন । ব্রিটিশদের রাজস্বনীতি, আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা ভারতের অর্থনীতির ওপর চরম আহাদাত হানে। রাজস্বনীতির ফলে অগণিত একসময়ের সমৃদ্ধ কৃষককুল মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বদায় হয়ে পড়ে। তারা ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রথমদিকে বাংলার বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষ্ণকদের কালর নূতন জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ প্রায় সীমা ছাড়িয়ে যায়ম। নূতন বিচারব্যবস্থা ছিল দরিদ্রের ওপর বিশেলীদের অত্যাচার ও শোষটার আর এক ব এছাড়া প্রশাসনের নিচুতলায় ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । সাধারণ পুলিশ, সামান্য কর্মচারি ও অধস্তন আদালতগুলি ছিল দুর্নীতিগ উইলিয়াম এডওয়ার্কস (William Edwards) নামে এক ইংরেজ কর্মচারি মহাবিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন- জনগণের প্রতি পুলিশ ছিল চাবুকস্বরূপ এবং তাদের অত্যাচার ও লোহল হিল সরকারের প্রতি অনগণের অসন্তোয়ের অন্যতম কারণ।
সামাজিক কারণেও ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, বিজিত ভারতবাসীর প্রতি বিজয়ী ব্রিটিশ শাসকবর্গের ঘৃণার মনোভাব ভারতবাসীর মনে গভীর বেদনার উদ্রেক করেছিল । ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দেয়ার-উল-মুতাশেরিন' নামে এক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে 'ইংরাজরা ইচ্ছা করেই ভারতবাসীর সংস্পর্শ বর্জন করে চলত।" স্যার সৈয়দ আহম্মদ খীও মন্তব্য করেছেন যে," এমনকি উঁচুপদের ভারতীয় কর্মচারি অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে ইংরাজ কর্মচারিদের সামনে যেতেন।" অবশ্য এর কারণ ছিল । সাধারণত ইংরাজরা ভারতীয়দের অশিক্ষিত বর্বর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না এবং খ্রীষ্টান পাদরিরা প্রকাশ্যেই হিন্দুদের মূর্তিপুজা ও সামাজিক কুসংস্কারের নিন্দা করত । ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস মন্তব্য করেছিলেন যে কিছুদিন আগেও ইংরাজরা অধিকাংশই ভারতীয়দের বর্বর মনে করত ৷ এইসব কারণে ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল যার প্রকাশ পায় মহাবিদ্রোহে ।
মহাবিদ্রোহের মূলে ধর্মীয় কারণও ছিল। বিদেশী ইংরাজদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি ও ভারতীয়দের ভা ধর্মের প্রতি নিয়ত কটাক্ষ ভারতীয়দের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল । শ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার, ভারতীয়দের ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা, শিখানায় কয়েদীদের কাছে প্রাস্টান পাদারদের অবিরত যাতারাত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আশঙ্কার সৃষ্টি করে যে ইংরাজদের উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করা । পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইবোজীকে প্রাধান্য দেওয়াতে রাহ্মণ ও মুসলিম মৌলভীরা যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন । ভারতীয় সংস্কারকদের পরামর্শে সরকার কতকগুলি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও গোঁড়াপন্থীরা তার বিরোধিতা করে । বর্মাজরিত হিন্দুর হিন্দুর পৈরিক পৈ সম্পত্তিতে অধিকার সংক্রান্ত আইন, রেলওয়ে ও টেলিগ্রামের প্রবর্তন, সতী-প্রথার। উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ আইন ইত্যাদি সনাতনপন্থী হিন্দুদের মনে আতছের সৃষ্টি করেছিল। মন্দির ও মসজিদের বাসজমির ওপর বাজনা ধার্য করে এবং ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলির ওপর কর ধার্য করে সরকার তারতীয়দের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সুতরাং তাঁদের ক্ষোভ বিদ্রোহের মুলে ইন্ধন জোগায় । এই ক্ষোভ থেকেই ওয়াহাবি আন্দোলনের এর উৎপত্তি হয়েছিল । ওয়াহাবিরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে এই আন্দোলনের সমর্থকরা যে অংশগ্রহণ করবে তা খুবই স্বাভাবিক।
উপরি উক্ত কারণগুলি এক ব্যাপক বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু যতদিন সিপাহীরা ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিল, ততদিন পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনগণ সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়াবার সুযোগ ও সাহস পায়নি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সিপাহীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিল, তারাও নানা কারণে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । প্রথমত, সিপাহীরা ছিল ভারতীয় সমাজেরই মানুষ এবং এই কারণে সমাজের অন্যান্যদের মতো তাদের মধ্যেও ক্ষেতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মতো সিপাহীরাও আর্থিক অভাব-অনটন থেকে মুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, কিছু ধর্মান্ধ ইংরাজ কর্মচারি সিপাহীদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে থাকায় তাদের মনে ধর্মচ্যুতির আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। সামরিক কর্তৃপক্ষ সিপাহীদের পক্ষে কপালে তিলক লেপন, দাড়ি রাখা ও পাগড়ী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করলে তাদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে যুগে সমুদ্রযাত্রা ছিল হিন্দুদের পক্ষে ধর্ম-বিরুদ্ধ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে সামরিক কারণে সিপাহীদের বহু দূর দেশে পাঠান হলে তারা অত্যন্ত দূর হয়। তৃতীয়ত, বেতনের ব্যাপারে ইংরাজ ও ভারতীয় সেনাদের মতো এক বিরাট বৈষম্য সিপাহীদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। পদোন্নতির ব্যাপারেও বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত। চতুর্থত, ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ খ্রীঃ) ও ভারতে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয় ভারতীয় সিপাহীদের মনে আশার সঞ্চার করে। ইতিমধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতি আদিম জাতিগুলির শৌর্যবীর্যের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ভারতীয় সিপাহীরা বুঝতে পারে যে ইংরাজরা অপরাজেয় নয়। ইংরেজদের বিতাড়িত করা যে কঠিন ব্যাপার নয়, সিপাহীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।