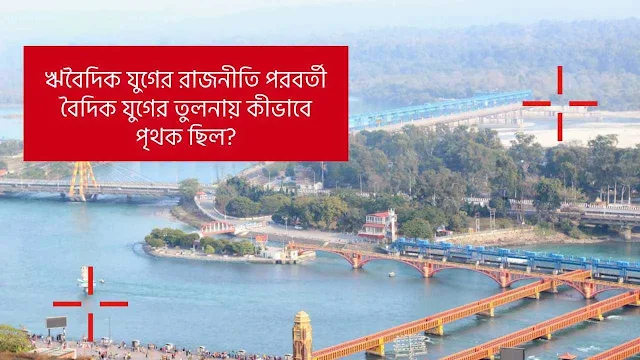ঋবৈদিক যুগের রাজনীতি পরবর্তী বৈদিক যুগের তুলনায় কীভাবে পৃথক ছিল?
আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ছিল ঋগ্বেদ। বাকি তিনটি বেদ অর্থাৎ সাম, যন্ত্র ও অথর্ব রচিত হয়েছিল ঋগ্বেদ রচনার বেশ কিছু পরে। ফলে ঋবৈদিক যুগে আর্যদের রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থনীতি যে ধরনের ছিল পরের বেদগুলি রচনার সময় তাতে বেশ কিছু
আপনি চাইলে এগুলো পড়তে পারেন
৩৬ পরিবর্তন সূচিত হয়। এইজন্যই সম্পূর্ণ বৈদিক যুগকে দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। তা হল ঋকবৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ। ঋগ্বেদের ঠিক গা থেকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সময়কে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা চলে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৬০০ • খ্রিস্টপূর্ব)। এই যুগ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের প্রধানত সাম, বন্ধু অথর্ব এই তিনটি বেদ এবং ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্যিক উপাদান ছাড়াও এই সময়ের ইতিহাস রচনার কাজে প্রশ্নতাত্ত্বিক উপাদানের কিছু সাহায্যও পাওয়া যায়। এই সকল উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে বিনাপুরে খননকার্যের ফলে।
প্রাপ্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা হয় যে, পরবর্তী বৈদিক যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে আর্যদের অগ্রগতি ঘটেছিল ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকা আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগেও আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ এক গোষ্ঠী বা উপজাতির সঙ্গে অপর কেন্দ্রী বা উপজাতির মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং বৃহৎ রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা দেখা যায়। পুরু ও ভরত এই দুটি গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরু উপজাতি এবং তুরবশ ও ক্রিবি উপজাতি দুটি যুগ্মভাবে পাঞ্চাল উপজাতি সৃষ্টি করেছিল। কুরু ও পাঞ্চাল উপজাতির সমন্বয়ের ফলে কুরু পাঞ্চাল উপজাতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। যা বৃহত্তর রাজ্য গঠনের ইঙ্গিত দেয়। এইভাবে একদিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের ধারণা স্পষ্টতর হতে থাকে। ড. এ. বি. কীথ অবশ্য এযুগে বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠনের ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, উপজাতি রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলেও, সাম্রাজ্যবাদের রূপ লাভ করেনি।
অথর্ব বেদের ভিত্তিতে ড. কীথের ঐ বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ বলে মনে হলেও তা সর্বাংশে সত্য নয়, কেননা ইতিহাসে বারেবারেই রাজরাজড়াদের সংঘর্ষের কাহিনি পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে, তারা সকলেই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত অভিধাগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা থেকে বোঝা সহজসাধ্য হবে যে পূর্বের জনপদভিত্তিক রাষ্ট্র এ যুগে ধীরে ধীরে ভূখণ্ড ভিত্তিক রাষ্ট্রের রূপ লাভ করছিল। এই গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে, পূর্ব ভারতের রাজারা 'সম্রাট', দক্ষিণ ভারতের রাজারা 'ভোজ', উত্তর ভারতের রাজারা 'বিরাট', পশ্চিম ভারতের রাজারা 'স্বরাট' এবং মধ্যপ্রদেশের রাজারা 'রাজন' উপাধিতে ভূষিত হতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, উপরে বর্ণিত ঐ সমস্ত দিকের রাজ্য যিনি জয় করবেন তিনি 'একরাট', 'সার্বভৌম', 'বিশ্বজনীন' প্রভৃতি অভিধা গ্রহণের যোগ্য। এই অভিধাগগুলি অর্জনের জন্য রাজারা রাজসূয়, রাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।
আপনি চাইলে এগুলো পড়তে পারেন
পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' রাজাকে সাক্ষাৎ ব্রয়ার প্রতিনিধি বলা হয়েছে। 'তৈত্তিরীয়' ব্রাহ্মণেও অনুরূপ মতের সমর্থন মেলে। সেখানে প্রজাপতি কর্তৃক রাজপদ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ফলে এযুগে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলের উপরেই রাজার ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছিল। এমনকী রাজা ইচ্ছামত অন্য সকলের উপর অত্যাচার ও শূদ্রকে হত্যা পর্যন্ত করার অধিকারী ছিলেন। রাজাকে বিভিন্ন সামরিক ও বিচারবিভাগীয় দায়িত কর্তবাও পালন করতে হত। রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে, রাজ্যের কৃষি, অর্থসম্পদ বৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি দায়বদ্ধ। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক সাধারণত ক্ষত্রিয় শ্রেণির মানুষই রাজা হতেন।
পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও, রাজার উপর যে জনগণের নিয়ন্ত্রণ ছিল তারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সৃঞ্জয়গণ তাদের রাজা দুষ্টঋতুকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল। অর্থাৎ, জনগণ রাজাকে পদচ্যুত করতে পারত। প্রজার প্রয়োজন হলে রাজাকে ধ্বংসকারী বিশেষ এক ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠান করত। অথর্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে, ঋগ্বেদিক যুগের মতো এ যুগেও 'সভা' ও 'সমিতি' নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। যদিও অনেকের মতে পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজক্ষমত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নতুন নতুন রাজকমচারী সৃষ্টি হবার ফলে এই যুগে সভা ও সমিতির প্রকৃত ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থার উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে 'ধর্মন'-এর উল্লেখ করা যায়। এই ধর্মন ব পবিত্র বিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ছিলেন একমাত্র মুনি-ঋষিরাই, রাজার এই অধিকার ছিল না।
রাজার ক্ষমতা ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল। 'পুরোহিত', 'সেনানী', 'গ্রামণী'-এই তিন ধরনের কর্মচারীর অস্তিত্ব ঋগ্বৈদিক যুগেও ছিল কিন্তু পরবর্তী বৈদিকযুগে বেশ কিছু নতুন কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'সংগ্রাহীতু' ও 'ভাগদুখ' উল্লেখযোগ্য, 'সংগ্রাহীতু' বলতে কোষাধ্যক্ষ এবং 'ভাগদুখ' বলতে রাজস্ব সংগ্রহকারীদের বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও সূত্র ক্ষত্রী, পালাগল, গো-বিকর্তন অক্ষ্যবাপ, সচিব প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।
পরবর্তী বৈদিক যুগে সেনানীর অস্তিত্ব নির্দেশ করে যে অন্তত অনিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হত। এরজন্য প্রয়োজনীয় ধনসম্পদ রাজা কৃষি অর্থনীতিজাত সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দলপতি শাসকের অন্যতম অভিধা বলিহৎ অর্থাৎ, যিনি বলি আহরণ করেন। ঋগবেদে 'বলি' শব্দের অর্থ দলপতি শাসকের উদ্দেশে কোথায় প্রদত্তসামগ্রী। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শব্দটির অর্থান্তর তার অর্থ শাসকের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক প্রদেয় সম্পদ। কিন্তু বলি নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট হারে আদায় করা কে কিনা তা জানা নেই। এই কারণে রোমিলা থাপার বলিকে শাসকের জন্য প্রদত্ত এনিয়মিত কিন্তু বাধ্যতামূলক সম্পদ হস্তান্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
পরবর্তী বৈদিক আমলে শাসক যেহেতু অনিয়মিত বলি আদায়ের মাধ্যমে বেশি সম্পদ গ্রহরণ করতে অক্ষম সেই কারণে শক্তিশালী সেনাবাহিনী রাখা শাসকের পক্ষে অসম্ভব। আবার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দমনের ব্যবস্থা না থাকায় রাজস্ব আহরণের জন্য চাপ সৃষ্টির কোনো উপায়ও শাসকের কাছে ছিল না। এই সমস্যার কারণে রাজার ক্ষমতার বৃদ্ধি উলেও পরবর্তী বৈদিক আমলে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর উদ্ভব হল না। অধ্যাপক অশরণ শর্মার মতে, এটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাক্কালের অবস্থা। রাষ্ট্রপ্রতীম রাজনৈতিক পরিস্থিতি থাকলেও বিকশিত রাজতন্ত্র তখনও অনাগত ৷