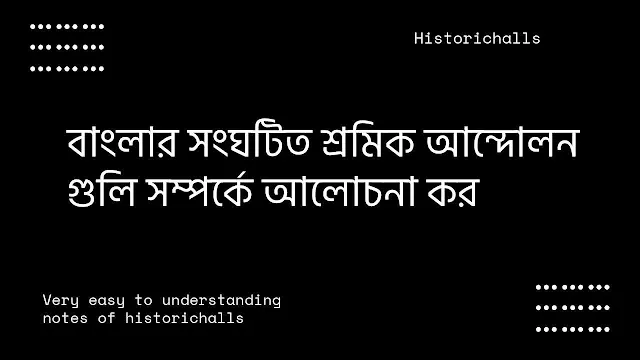বাংলার সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলন গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর
ভারতের আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই শতকের শেষ দিকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার ও সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বাংলায় শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে প্রথম উৎসাহ দেখান জনৈক্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক শশীপদ ব্যানার্জি। তার উদ্যোগে 'শ্রমজীবী সংঘ' নামে শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার প্রসারে উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা এবং জাতীয় আন্দোলন শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। দাদাভাই নৌরজি জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে কংগ্রেস কেবল সেইসব বিষয়ের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে যেগুলোতে সমগ্র জাতি অংশগ্রহণ করতে পারবে। শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্কে জাতীয় নেতৃত্বের এই সচেতন উদাসীনতা ভারতের সংঘটিত শ্রমিক জাগরণের সম্ভাবনাকে অনেকটাই পিছিয়ে দেয়।
বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ক্ষোভকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয় করে তোলার একটা প্রয়াস দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি নেতাদের কেউ কেউ শ্রমিকদের সংঘটিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল যেমন প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্ব কুমার ঘোষ প্রমুখ। শ্রমিক সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে এরা মূলত বেছে নিয়েছিল ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োজিত কারখানা গুলি। এই সময় বাংলাদেশের বহু চটকলে অর্থনৈতিক দাবীতে শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।
১৯০৮ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে শ্রমিক আন্দোলনের কম তীব্রতা দেখা যায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসদের উদ্যোগে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গঠিত হলে বাংলাদেশসহ সারাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন গতিবেগ আসে। বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের ১৯২০-১৯২২ সময়কালে তীব্রতর হওয়ার পশ্চাত্পটে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রুশ বিপ্লব এবং বিশ্বযুদ্ধত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক আর এ বৃদ্ধি পায়। মজুরি বৃদ্ধি, বাসস্থান, চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি দাবিতে তারা বারবার বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়।
বাংলায় শ্রমিকদের সংগঠিত করার কৃতিত্ব প্রথম স্বরাজ দলের প্রাপ্য। স্বরাজ দল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। সর্বভারতীয় রেল কর্মচারী ইউনিয়ন গঠনে তিনি যুক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন এর সহযোগী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি লেবার কমিটি গঠন করলে বাংলায় শ্রমিক সংগঠনের নতুন গতিবেগ আসে।
১৯২০-২২ সময়কালে শ্রমিক অসন্তোষক আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। কলকাতা, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল এবং হুগলি তীরবর্তী পাটকল গুলিতে 30 টির বেশি ধর্মঘট পালিত হয়। গৌরীপুর ও ওয়েলিংটন পাটকলের শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের দূরব্যবহারের প্রতিবাদ করাকেই ধর্মঘটের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসামে শ্রমিকদের ওপর পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদী পূর্ববঙ্গের, নোয়াখালী, শিলচর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য শহরের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনাতেও শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটে শামিল হন।
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর 1922-27 খ্রিস্টাব্দের অন্তবর্তিকালে অন্যান্য রাজ্যের মত বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে ভাটা দেখা যায়। এই সময় শ্রমিক আন্দোলন গুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই পর্বে আন্দোলনের নেতৃত্বে শ্রমিকদের সক্রিয় বা কার্যকরী ভূমিকা ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণ ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের সংগঠিত করে শ্রেণীগত আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি হাজির করলে বাংলা সহ নানা দেশে নব রূপে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে।
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের শ্রমিকদের আর্থসামাজিক স্বপ্ন পূরণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কমিউনিস্টরা ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিন্যাসের রূপান্তরের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যের শ্রমিকদের আন্দোলনমুখী করতে উদ্যোগী হন। শ্রমিক আন্দোলনে আপোষমূলক সমঝোতা তত্ত্ব বর্জন করে সর্বাত্মক সংগ্রামের বলশেভিক তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়। তবে সরকার 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন আক্ট'জারি করে আগেভাগেই শ্রমিকদের আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার অভিসন্ধি করেন। দমনমূলক ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ট্রেড ডিসপিউট আক্ট' এবং পাবলিক সেফটি আক্ট' পাশ করানো হয়। সরকার শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা ও কার্যকলাপ কে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারের এই অন্যায় মিথ্যাচার ও দমনমূলক মনোভাবের প্রকাশ ঘটে।
ওয়াকার্স এন্ড পেসেন্ট পার্টি বা শ্রমিক কৃষক দল প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট মত ও পথের প্রভাব ঘটে। এই দলের উৎস জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক স্বরাজ দলের মধ্যে নিহিত। কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার প্রমুখ ছিলেন এই দলের রূপকার। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের 'শ্রমিক কৃষক দলের' আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিক ও কৃষকদলের উদ্যোগে সারা বাংলায় চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। সাধিত হয় বাংলা পাট শ্রমিক সংঘ।
১৯২৭ থেকে ৩০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বাংলায় উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ ও চটকল শ্রমিকদের প্রতিবাদী ধর্মঘট। প্রথমে শ্রমিক কর্মচারীরা টানা 26 দিন ধর্মঘট পালন করে। সরকারের প্রচন্ড দমনপিড়নের ফলে আন্দোলনকারীরা ধর্মঘট তুলে নেয়। 1700 শ্রমিকদের ওপর ছাটাই নোটিশ জারি করা হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ইস্ট ইন্ডিয়ান ও সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘটে সামিল হন। পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ করলে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জুলাই মাসে সাউথ ইন্ডিয়ান রেল কর্মচারীরা রেল চলাচল প্রায় অচল করে দেন। ভীত ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চট্টিয়ার এবং মুকুন্দলাল সরকারকে গ্রেফতার করে।
১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কর্মচারী শ্রমিক শোষণের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এই সময় বাংলার চটকল মালিকরা সপ্তাহের কাজের সময়সীমা ৫৪ ঘন্টা থেকে বাড়ি এ ৬০ ঘন্টা করে দেয়। তবে শ্রমিকদের মজুরি একই থাকে এর প্রতিবাদে ১৯২৯ জুলাই মাসে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধর্মঘটের ডাক দেন। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনা এই আন্দোলন সর্বাত্মক ধর্মঘটের রূপ নেয়। শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে কাজের সময়সীমার নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেন।উপরন্তু মিল মালিকরা পাটকলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে স্বীকৃতি দেন।
১৯২৯-৩৫ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির অন্তদ্বন্দ্বের কারণে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে ভাঙ্গন দেখা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে দ্বন্দ্ব প্রকাশে চলে আসে। ওই বছর ডিসেম্বরে নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে এই বিরোধিতা চরমে ওঠে। সংস্কারপন্থি এম. এন.জোশি, ভি.ভি গিরি প্রমূখ আই.টি.ইউ.সি ত্যাগ করে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে।
শেষ পর্যন্ত 1935 খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত এ.আই. টি. ইউ.সি এর অধিবেশনে নীতিগত বিরোধের মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই বছরে এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে রেড ট্রেড ইউনিয়ন ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন আবার মিলিত হয়ে যায়।
১৯৩৫ এ ঘোষিত হয় নতুন ভারত শাসন আইন।এতে আইন সভা গুলিতে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। একই সময় অর্থনৈতিক মন্দার অবসান ঘটলে শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করার সুযোগ আসে ফলে কমিউনিস্টরাও তাদের রাজনৈতিক কৌশলে পরিবর্তন আনে। এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন জানান। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তবে বাংলাদেশের ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাপাটি সরকার গঠন করে।
১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার চটকল শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে স্বদেশীয় প্রাদেশিক সরকার তাদের দাবি সমূহ বিবেচনা করবেন। দুর্ভাগ্যবশত ফজলুল হক সরকার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের ন্যায্যতা অস্বীকার করেন। এবং দমন চালিয়ে আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন সমাজিক শক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কং গ্রেসের ওয়াকিং কমিটি চটকল শ্রমিকদের সমর্থন জানায়। বাংলার ছাত্রসমাজ শ্রমিকদের জন্য রিলিফ ফান্ড গঠন করে। শেষ পর্যন্ত সরকার নম্র হয় এবং ধর্মঘটের নেতাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তাদের কিছু দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৩৭ এর মে মাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। তবে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে কৌশলগত মতভেদের কারণে কোন সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়নি।
৩০-এর দশক থেকে বাংলার বামপন্থী ও কমিউনিস্ট রাজনীতিতে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, ছাড়াও লেভার পার্টি, কমিউনিস্ট লীগ অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি ছোট ছোট দল গড়ে উঠেছিল। সর্বভারতীয় সংগঠন বলে দাবি করা হলেও এদের প্রভাব মূলত বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। একদিকে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল অন্যদিকে কর্মসূচি গত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।
১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। রাজনৈতিক অসন্তোষের পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক অসন্তোষ ও বাড়তে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে শ্রমিকদের আয় কমতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে হয়েছিল ৭৪.৯%। অন্যদিকে পাটকল মালিকদের আয়ের সূচক বেড়ে হয়েছিল ৩২৭.৬ শতাংশ। সরকার চাইছিল কলকারখানায় উৎপাদন অব্যাহত থাকুক। তাই সরকার দুমুখী নীতি নেয়। 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলস', 'ন্যাশনাল সার্ভিস আর্ডন্যান্স' ইত্যাদি কঠোর নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন জারি করে।
অন্যদিকে শিল্প মালিকদের সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতার পথ থেকে উৎপাদন অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেয়, ফলে শ্রমিকদের পক্ষে সংগঠিত বৃহত্তর কোন আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বাংলার শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে ভাঙ্গনও শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে 'বেঙ্গল জুট ওয়ারকার্স ইউনিয়ন' ভেঙ্গে গিয়েছিল কমিউনিস্টদের একটি গোষ্ঠী 'বেঙ্গল চটকল মজনুর ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।
এত অস্থিরতার মাঝে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বাংলায় কৃষকরা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও আন্দোলন মুখী ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বহু চটকলের শ্রমিকরা, ইতিপূর্বে হ্রাস করা বেতন পুনরায় চালু করার দাবিতে ধর্মঘট করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশনের ২০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী মহার্ঘভাতা (DA)-র দাবিতে ধর্মঘটে নামেন। ১৯৪০-৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনার চটকল গুলিতে মহার্ঘভাতার দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন সংঘটিত করেন। জুতো কারখানা, ইলেকট্রিক ওয়ার্কার ও স্টিল কারখানার শ্রমিকরা, বোনাসের দাবিতে আন্দোলন করেন।
ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্কালে কলকাতায় ট্রাম পরিবহন শ্রমিক কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা ও বরখাস্ত সহকর্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেন। ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে সরকার গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলে বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক শ্রেণী যে প্রতিক্রিয়া দেখায় বাংলায় তা দেখা যায়নি। ১৯৪২-১৯৪৫ সময়কালে বাংলার বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলন গুলিতে অর্থনৈতিক দাবিই প্রাধান্য পেয়েছিল রাজনৈতিক নয়।
স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বাংলায় আবার শ্রমিক আন্দোলনের তেজীভাব দেখা যায়। এই সময় কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট, বন্দর কর্মী ধর্মঘট ও দার্জিলিংয়ের চা বাগিচা শ্রমিকদের আন্দোলন ইত্যাদি সংঘটিত হয়। ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে শ্রমিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে।
তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাংলার সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলন গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর এই নোটটি পড়ার জন্য